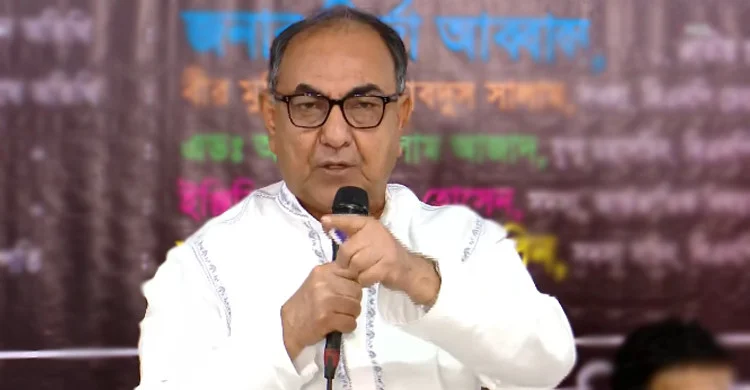দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীলতার নেপথ্যে প্রধান অনুঘটক জলবায়ু পরিবর্তন
- আপডেট সময়ঃ ০৮:২০:৩৭ অপরাহ্ন, শনিবার, ২২ জানুয়ারী ২০২২
- / ২৭১ বার পড়া হয়েছে
নিজস্ব প্রতিবেদক :
দ্রব্যমূল্যের দাম লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে। দ্রব্যমূল্যের এই লাগামহীন বাজারে লাগাম পরানো যাচ্ছে না কোনভাবেই। শীতের ভর মৌসুমেও সবজি বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে এলপিজি (রান্নার) গ্যাসসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। বর্তমানে নতুন করে পেঁয়াজের ঝাঁঝ বাড়ছে। ভুক্তভোগীরা দ্রব্যমূল্য আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন এবং এজন্য তারা সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর বাজার তদারকির কথা বলছেন। এটি স্পষ্ট যে, নিত্যপণ্যের বাজারদরের সাথে আসলে আরও অনেক বিষয় জড়িত। বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আরও নানা সমস্যা দেখা দেবে বলে। নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে না থাকলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। মজুতদার ও লোভী ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো অবস্থা হলেও খুচরা ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কষ্ট দিন দিন বাড়তে থাকবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন অল্প বেতনের সৎ সরকারি-বেসরকারি কর্মকতা-কর্মচারী, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী। যেসব চাকরিজীবী সৎভাবে জীবন কাটান, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রবীণ জনগোষ্ঠীসহ নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তারা। জানা যায়, করোনা পরিস্থিতির পূর্বে বাজার বেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খাদ্যমূল্য বলতে গেলে তুলনামূলক কম এবং স্থির ছিল। কিন্তু ২০২১ সালে গড়ে বৃদ্ধি পায় ২৮ শতাংশ। এর নেপথ্য কারণ ভুট্টা ও গমজাতীয় খাদ্যসহ সিরিয়ালের (বিভিন্ন শস্যদানা দিয়ে তৈরি খাবার, যা সকালের নাশতায় খাওয়া হয়) দাম ৪৪ থেকে ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি। এ ছাড়া দাম বেড়েছে অন্যান্য খাদ্যপণ্যেরও। বিদায়ী বছর ভেজিটেবল অয়েলের দাম রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। চিনির দাম বাড়ে ৩৮ শতাংশ। মাংস ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যের দাম তুলনামূলক কম থাকলেও ডাবল ডিজিট থেকে সিঙ্গেল ডিজিটে নামেনি। খাদ্য মূল্যস্ফীতি বর্তমানে সামগ্রিক মূল্যসূচকের বৃদ্ধি ছাড়িয়ে গেছে। কভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন শ্রমিকদের মজুরি আয়ের উল্লেখযোগ্য হ্রাসের কারণে এটি আরো উদ্বেগজনক, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয়। অধিক ব্যয়বহুল খাদ্যের এ প্রাণঘাতী সংমিশ্রণ এবং নিম্ন আয় ক্ষুধা ও অপুষ্টিকে বিপর্যয়কর অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। খাবারের দাম বাড়ার সম্ভাব্য কারণ কিন্তু অনেক, যার কিছুটা পদ্ধতিগত। যেমন সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যা, বিশেষ করে পরিবহনসংক্রান্ত, যা পণ্যের বিস্তৃত পরিসরে মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে। তবে ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন টন রেকর্ড পরিমাণ বৈশ্বিক উৎপাদন সত্ত্বেও ২০২১ সালে শস্যের দাম অনেক বেশি দ্রুত হারে বেড়েছে। তাছাড়া শস্য উৎপাদন ও পরিবহন খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জ¦ালানির মূল্যও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সালে তেলের দামের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে ভোক্তাদের খাদ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শস্য উৎপাদন বাধাগ্রস্ত ও হ্রাস পাচ্ছে।
এদিকে কেউ কেউ অবশ্য যুক্তি দেখাচ্ছেন যে ২০২১ সালে জলবায়ু পরিবর্তন উৎপাদনকে প্রভাবিত করার কারণে কৃষিপণ্যের দাম ঠিক ব্রাজিলিয়ান কফি, বেলজিয়ামের আলু কিংবা কানাডিয়ান হলুদ মটরের (বর্তমানে মাংসের বিকল্প হিসেবে উদ্ভিদভিত্তিক এ খাবারগুলো ব্যাপক হারে ব্যবহার হচ্ছে) মতো পণ্যের মূল্য দ্রুত ও অসমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কৃষির সাথে জলবায়ুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য অনুকূল জলবায়ু অপরিহার্য। ২০২১ সালের মার্চে এফএও সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে কৃষি সরবরাহকে প্রভাবিত করছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত বিপর্যয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বৃহৎ হুমকি হয়ে এসেছে খরা। যা নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোয় ফসল ও গবাদি পশুর এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতির জন্য দায়ী। কিন্তু বন্যা, ঝড়, পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং বনাঞ্চলে দাবানলের ঘটনাগুলো আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ও ব্যাপক আকারে ঘটছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরে খাদ্য উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনগত প্রভাব আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলেই অনুমেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রধানত উন্নত দেশগুলো। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল তারা খুব একটা ভোগ করবে না, কেননা তাদের হাতে আছে শক্তিশালী অর্থনীতি। ভুক্তভোগী হিসেবে পরিগণিত হবে অনুন্নত ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার মতো উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও আঘাতের মাত্রা বেশি হবে। এ অবস্থায় জলবায়ু ঝুঁকি থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদনের হুমকি বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং এর পরিণতি মোকাবেলায় বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। দুঃখজনকভাবে, সার্বিক পরিস্থিতি দেখে এ ধরনের সহযোগিতার বিষয়গুলো অনেকটা অসম্ভাব্যই মনে হয়। বিশেষ করে বিশ্বনেতাদের অবস্থান, নীতিনির্ধারণে অপারগতা বা এ-বিষয়ক মতানৈক্যে পৌঁছার অপারগতার কথা যদি বিবেচনা করা যায় তবে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখে এমন কয়েকটি কারণের মধ্যে রয়েছে নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন। যেমন কভিড-১৯-এর ঊর্ধ্বগতি আবারো হয়তো খাদ্য সরবরাহকে চাপের মুখে ফেলতে পারেÑএ ধরনের ভয় থেকে সরকার ও ভোক্তা দ্বারা উল্লেখযোগ্য হারে মজুদ বৃদ্ধির মতো ঘটনা ঘটে। অতিরিক্ত চাহিদার কারণে ভবিষ্যতে খাদ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি তখন অনেকটাই প্রত্যাশিত ঘটনা হয়ে আসে। গত নভেম্বরে এফএও তাদের এক হিসাবে দেখিয়েছে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য আমদানির ব্যয় ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১ দশমিক ৭৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যা ২০২০ সালের চেয়ে ১৪ শতাংশ এবং এফএওর অনুমানের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। এটি যে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য অশনি সংকেত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা অন্যান্য দেশের তুলনায় খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা যেমন বেশি হতে পারে, আবার চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই তারা বৈশ্বিক বাজার থেকে ছিটকে যেতে পারে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে খাদ্যপণ্যের বাজার সম্পর্কিত আর্থিক অনুমান, যা সম্প্রতি পুনর্জাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। চলতি শতকের শূন্য দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক নিয়ন্ত্রণহীনতার পর খাদ্যদ্রব্য রীতিমতো উচ্চসম্পদে পরিণত হয়। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য-প্রমাণও রয়েছে যে বিষয়টি ২০০৭-০৯ সাল পর্যন্ত খাদ্যপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার নেপথ্যে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় খাদ্যপণ্য বিনিয়োগকারীদের কাছে খানিকটা কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে মহামারী শুরুর পর এ ধারণা বদলে যায় বলে জানা যায়। বৈশ্বিক বাজার থেকে বাংলাদেশ যাতে ছিটকে না পড়ে এজন্য এখন থেকেই বাজার নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দেখা যায় তা হলো একবার যে পণ্যের দাম বাড়ে, সাধারণত তা আর কমে না। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করলেও কিছুতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আসছে না। দ্রব্যমূল্য দেখভাল করতে ‘কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ (ক্যাব) নামে একটি সংস্থা রয়েছে। তাদের কার্যক্রম আরও গতিশীল করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।